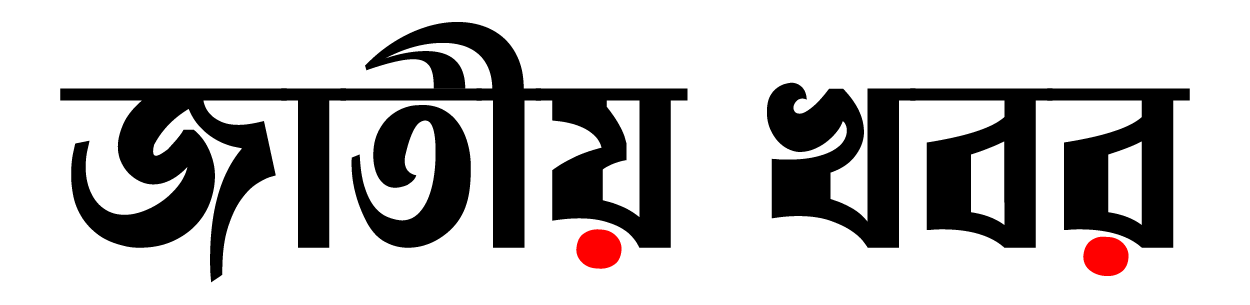অর্থনীতির মন্দা ও পুনরুদ্ধার নিয়ে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মিলটন ফ্রিডম্যানের একটি বিখ্যাত তত্ত্ব আছে—“গিটার স্ট্রিং থিওরি অব রিসেশনস।” এর ব্যাখ্যা হলো, গিটারের একটি তারকে যদি নিচে টেনে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেটি দ্রুত আগের অবস্থায় ফিরে আসে। ফ্রিডম্যানের মতে, অর্থনীতিও ঠিক এমনই—মন্দায় যখন সবকিছু নিচে নেমে যায়, মন্দার কারণ দূর হলে অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায়। অর্থাৎ, যত গভীর মন্দা, পুনরুদ্ধারও তত দ্রুত হওয়ার কথা।
তবে এই তত্ত্ব প্রথম প্রশ্নবিদ্ধ হয় ২০০৮–০৯ সালের বৈশ্বিক মন্দার সময়। তখন দেখা যায়, বিশ্ব অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি; বরং পুনরুদ্ধার ছিল ধীর, দুর্বল ও অসম। অর্থনীতিবিদেরা ব্যাখ্যা করেন—মন্দা কখনো এত গভীর হয় যে “গিটারের তার ছিঁড়ে যায়”, অর্থাৎ অর্থনীতির কাঠামোগত ক্ষতি এমন হয় যে দ্রুত পুনরুদ্ধার অসম্ভব হয়ে পড়ে।
বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত বেসরকারি খাতনির্ভর। ফলে বিনিয়োগ না বাড়লে কর্মসংস্থান ও আয়—দুটিই স্থবির থাকে। সরকারি হিসাবেই দেখা যাচ্ছে, মানুষের প্রকৃত আয় কমেছে, কারণ মজুরি বৃদ্ধি মূল্যস্ফীতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি। এদিকে ৫০ হাজারেরও বেশি শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন।
২০২০ সাল থেকে বাংলাদেশ কার্যত মন্দায় আছে। প্রথমে কোভিড-১৯, পরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ—এই দুই ধাক্কায় বিশ্ব অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়, তবে অধিকাংশ দেশই এখন পুনরুদ্ধার করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ এখনো পারেনি। বিশ্লেষকদের মতে, সাবেক আওয়ামী লীগ সরকার সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নষ্ট করে “তারটা ছিঁড়ে ফেলেছিল।” দুর্নীতি, অর্থ পাচার, টাকার অবমূল্যায়ন, খেলাপি ঋণ, রিজার্ভ পতন—সবই সেই সময়ের ফল।
অন্তর্বর্তী সরকার এসে রিজার্ভ পতন ঠেকাতে কিছুটা সফল হয়েছে। বর্তমানে রিজার্ভ ৩২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে, ডলারের দরও স্থিতিশীল। প্রবাসী আয় ও রপ্তানিই মূল ভরসা। তবে সামষ্টিক অর্থনীতি কিছুটা স্থিতিশীল হলেও বিনিয়োগে কোনো গতি আসেনি। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি মাত্র ৬.৩৮ শতাংশ—যা বিনিয়োগে স্থবিরতার প্রমাণ।
সরকারি সংস্থা বিবিএস সর্বশেষ দারিদ্র্যের হার নির্ধারণ করেছিল ২০২২ সালে—১৮.৭ শতাংশ। কিন্তু বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পিপিআরসি বলছে, এখন তা বেড়ে ২৭.৯৩ শতাংশে পৌঁছেছে, আরও ১৮ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে আছে। অর্থাৎ দারিদ্র্য এখনো বাংলাদেশের বাস্তব চিত্রের অংশ।
প্রশ্ন হচ্ছে—অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব কি? ইতিহাস বলছে, তত্ত্বাবধায়ক ধরনের সরকারগুলো সাধারণত নিরপেক্ষ থাকে, দুর্নীতি কমায়, আইনশৃঙ্খলা ভালো রাখে। কিন্তু এবার তা হয়নি। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও চাঁদাবাজি বিনিয়োগকারীদের আস্থা নষ্ট করেছে, নির্বাচনী অনিশ্চয়তা তা আরও বাড়িয়েছে।
এমন পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদ নিকোলাস ব্লুম ও তাঁর সহকর্মীদের গবেষণাটি প্রাসঙ্গিক। তাঁরা বলেন—নীতি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয় ও সন্দেহ থেকেই অনিশ্চয়তার জন্ম হয়; যখন অনিশ্চয়তা বাড়ে, ব্যবসা-বিনিয়োগ, নিয়োগ ও ব্যয়—সব কিছুই স্থবির হয়ে পড়ে, ফলে প্রবৃদ্ধি কমে যায়। বাংলাদেশের বর্তমান চিত্রও এরই প্রতিফলন।
তাহলে সমাধান কী?
প্রথমত, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা দূর করতে হবে। বাংলাদেশ টানা পাঁচ বছর ধরে অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে আছে। এখন দরকার একটি বিশ্বস্ত নির্বাচন, যা আস্থা ফিরিয়ে আনবে। নির্বাচনের পর নতুন সরকার যদি দক্ষতার সঙ্গে দুর্নীতি দমন, ব্যাংক খাত সংস্কার, অবকাঠামো উন্নয়ন ও চাঁদাবাজি বন্ধ করতে পারে, তবে অর্থনীতির পুনরুদ্ধারও ত্বরান্বিত হবে।
নিকোলাস ব্লুম তাঁর গবেষণায় বলেছিলেন—‘অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা’ কথাটি গণমাধ্যমে যতবার ব্যবহৃত হয়, তা অনিশ্চয়তার সূচক হতে পারে। এই লেখায় সে শব্দটি বহুবার এসেছে—এখন দেখার বিষয়, কবে এই শব্দটি আর ব্যবহৃত হবে না। হয় অনিশ্চয়তা দূর হবে, নয়তো বলা নিষিদ্ধ হবে। দেখা যাক, কোনটি আগে ঘটে।