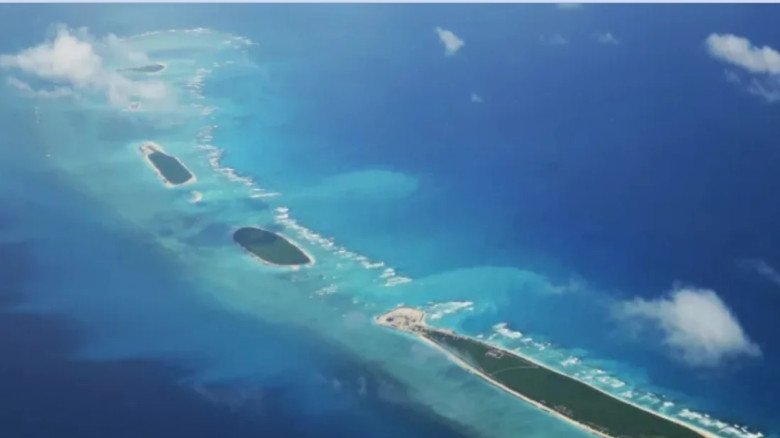আমাদের গ্রামের বাড়ি সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার মাটিয়াপুরে। স্কুলজীবনটা সুনামগঞ্জেই কেটেছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় শেষে দীর্ঘ কর্মজীবনও শেষ করেছি। জীবনের কতটা পথ পার হয়ে এলাম। আজ কত কথা মনে পড়ে।
তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। পত্রিকায় নিজের নামটা ছাপার অক্ষরে একটু দেখতে পেলে মহা আনন্দিত হই। সাধ্য তো ছিল ওইটুকুই, দৈনিক আজাদ পত্রিকার মুকুলের মহফিলে বাগবান অথবা কচি-কাঁচার আসরে দাদাভাইকে চিঠি লেখা। সব সময় যে উত্তর পাওয়া যেত তা নয়, কিন্তু যেদিন পাওয়া যেত, সেদিন আর আমাকে পায় কে? মর্নিং নিউজ-এর ছোটদের পাতায় শুধু পেন পল ঘেঁটে কলমবন্ধুত্বের জন্য লিখতাম। একবার রেডিও পাকিস্তান, ঢাকার ছোটদের অনুষ্ঠানে কবি ফররুখ আহমদ আমার চিঠির জবাব দিলেন। নিজের নাম ওনার মুখে শুনে জীবন ধন্য হয়ে গেল!
কিছুদিন পর একসময় মনে হলো, নাহ্, এবার একটা গল্প লিখে পত্রিকায় পাঠাই না কেন। তারপর ভাইবোনদের নজর এড়িয়ে চুপিসারে একটা গল্প লিখে ডাক বিভাগের ছোট হলুদ খামে ঠেসেঠুসে ভরে মুকুলের মহফিলে পাঠিয়ে দিলাম। বাগবানকে এটাও লিখে দিলাম, গল্প যদি ছাপার যোগ্য না হয়, প্লিজ চিঠিতে উল্লেখ করবেন না। এত সব গোপনীয়তার কারণ হলো, ছাপা না হলে আমার আগে-পিছে দুটো দুটো চারটা ভাইবোনের ঠাট্টা-মশকরার শিকার হতে হবে।
তখন সোম অথবা মঙ্গলবারে মুকুলের মহফিল প্রকাশিত হতো আর সুনামগঞ্জে আমরা পত্রিকা পেতাম পরের দিন বিকেলে। একদিন একটা গল্প পাঠিয়ে আমি যথারীতি হাপিত্যেশ করছি! প্রথম সপ্তাহে গল্প ছাপা হলো না। দ্বিতীয় সপ্তাহেও একই অবস্থা। আমার অপেক্ষার রেলগাড়ি আর চলছে না! তৃতীয় সপ্তাহে মঙ্গলবার তিনটা থেকেই আমি ঘর-বাহির করছি। আম্মা বললেন, ‘তোমার আবার কী হলো?’ আমি বললাম, ‘মাথাব্যথা’।
পাঁচটা বেজে গেল। সেদিন খাটো ধুতি, নীল নিমা পরা ঠাকুর (হকারের নাম ছিল ঠাকুর) আর এলেনই না! আমি ধপাস করে গিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকলাম। পরের দিন ঠাকুর আসতেই আমি গিয়ে হামলে পড়লাম। ‘গতকালের পত্রিকা যে দিলেন না?’ ‘খেনে দিদি, আফনারার আদমের খাছে তো দিয়া দিছি’, চিরাচরিত মৃদু হাসির সঙ্গে ঠাকুরের জবাব।
তক্ষুনি খোঁজ খোঁজ!
‘আন্দা (আদম দাদার সংক্ষিপ্তি), পত্রিকা কই?’
‘বইনে আমার গরো আছে।’
‘জলদি নিয়ে আয়।’
দলামোচা পাকানো পেপারটার অবস্থা দেখে আমি হতবাক!
‘বইনে, এখ আটি লাখরি ফেছাইয়া আনছিলাম, শার্টটা নষ্ট অই যাইব খইরা।’
মাথানত অবস্থায় অত্যন্ত কুণ্ঠিত আন্দার জবাব।
টেবিলে রেখে অতি কষ্টে আঙুল দিয়ে চেপে চেপে ঠিক করার পরে দেখলাম, আমার গল্পটা ঠিকই ছাপা হয়েছে! পেপারটা দোমড়ানো, কোঁচকানো থাকলেও ওটাতে ওই মুহূর্তে আমার নামটা আমার কাছে হীরককুচির মতোই ঝকমক করতে লাগল। আহা কী আনন্দ!
আরেকটি ঘটনা লিখতে মন চাইছে। তখন ক্লাস ফোর অথবা ফাইভে পড়ি। স্টেশন রোড (বর্তমান মেজর ইকবাল রোড) ধরে ডান দিকে মোড় নিয়ে কালীবাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে স্কুলে যেতাম। কালীবাড়ির রাস্তায় মোড় নিলেই দেখা যেত, ডান দিকের ছোট্ট একটা ঘরে একজন বয়সী মানুষ আসন করে বসে রোজ সুর করে রামায়ণ অথবা মহাভারত পড়ছেন। তার পরের ঘরগুলোতে দুই ঘোষ দম্পতি পরিবার-পরিজনসহ থাকত। ঘোষ জায়াদের বড়জন একটু ফরসা, পৃথুলা ধরনের ছিলেন। প্রায়ই দেখা যেত, সংসার সামলাতে গিয়ে তিনি ঘেমেনেয়ে একাকার হয়ে আছেন। ছোটজন ছিলেন শ্যামলা, মিষ্টি চেহারার। সম্ভবত তিনি একটু মৃদুভাষীও ছিলেন। ওই দিকটা দই, মাঠা, মাখনের গন্ধে মাখামাখি হয়ে থাকত।
স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে সবকিছু হাঁ করে দেখা ছিল আমার স্বভাব। ওনাদের ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার চলার গতি শূন্য স্পিডে নেমে আসত। ঘরের ভেতরে দইয়ের ভাণ্ডে লম্বা বাঁশের কুরা (ঘুঁটনি) ঢুকিয়ে, ওটাতে লম্বা দড়ি পেঁচিয়ে একবার ডানে, একবার বাঁয়ে হ্যাঁচকা টান দিয়ে দিয়ে ঘুঁটে ঘুঁটে মাখন বের করা, মাঠা বানানো আমি মুগ্ধ হয়ে দেখতাম।
তো একদিন ওনাদের ঘরের সামনে মাত্র এসেছি। হঠাৎ কী একটা থপ করে এসে সামনে পড়ল! আমরা ভয়ে তিন পা পিছিয়ে গেলাম। দইয়ে মাখামাখি বস্তুটা যখন নড়ে উঠল, দেখি বিশাল এক কোলা ব্যাঙ! দইয়ের ভাণ্ডে শোবার শান্তি বিঘ্নিত হওয়ায় সে-ও মহাবিরক্ত! গলার দিকটা লকলক করছে আর মার্বেল চোখে তাকানোর চেষ্টা করছে! বড় গিন্নির ঝাঁটার বাড়ি একটা পড়তেই দক্ষ অ্যাক্রোবেটের মতোই পাশে পুকুরপাড়ের কচুবনে দু-তিন লাফে হাওয়া হয়ে গেল! এই ঘটনা বহুদিন ধরে আমাদের হাসি এবং অস্বস্তির খোরাক হয়ে থাকল।
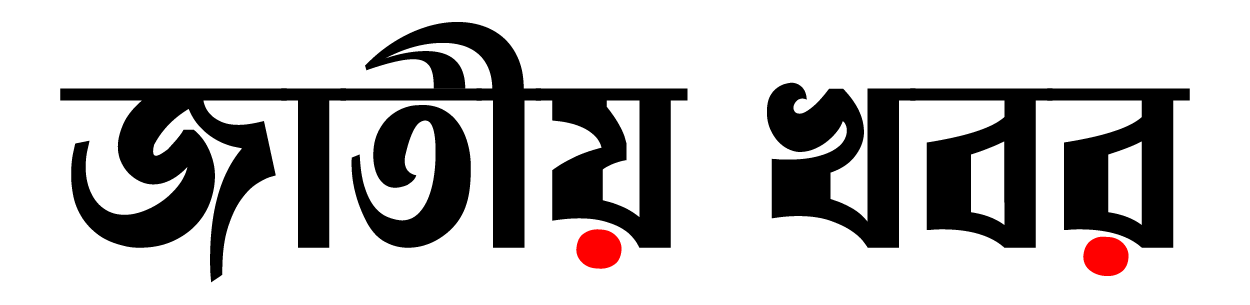


 Jatio Khobor
Jatio Khobor